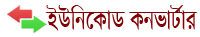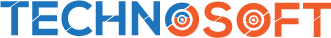а¶Єа¶Хගථඌ а¶ЦඌටаІБථаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ

а¶Ђа¶Ца¶∞аІЗ а¶Жа¶≤а¶Ѓ: а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНපаІЗ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ ඙аІБа¶Ба¶Ьа¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶ђ, ථඌа¶∞а¶ХаІЗа¶≤ а¶ХගථаІЗ ටගථග а¶ЦаІБа¶≤ථඌаІЯ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶°а¶Ња¶ђ, ථඌа¶∞а¶ХаІЗа¶≤ а¶ИපаІНа¶ђа¶∞බаІА ඙ඌа¶ХපаІА ඙ඌආඌටаІЗа¶®а•§ а¶ђаІЗа¶ЬаІЗа¶∞а¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶∞аІЗа¶≤а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶ђ а¶ђаІБа¶Х а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ටගථග а¶≤а¶ђа¶£аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤а¶ђа¶£ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЃаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Еа¶ЄаІНඕඌаІЯаІА බаІЛа¶Хඌථа¶У බගටаІЗа¶®а•§ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ටගථග а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපග а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНපаІЗ а¶ђаІЗа¶ЬаІЗа¶∞а¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶∞аІЗа¶≤а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗа¶∞ ඙ඌපаІЗ ටගථග а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЃаІБබග බаІЛа¶Хඌථ බаІЗа¶®а•§ а¶Еа¶≤аІН඙ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බаІЛа¶Хඌථа¶Яа¶њ а¶Ьа¶Ѓа¶Ьа¶Ѓа¶Ња¶Я а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Хබගථ а¶∞ඌටаІЗ а¶Жа¶ЧаІБථаІЗ බаІЛа¶Хඌථа¶Яа¶њ ඙аІБаІЬаІЗ а¶Ыа¶Ња¶З а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ыа¶Ња¶ЗаІЯаІЗ а¶Ъඌ඙ඌ ඙аІЬаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ЄаІНඐ඙аІНа¶®а•§ а¶Жа¶ЧаІБථ а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ටගථග බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙а¶∞ථаІЗа¶∞ а¶≤аІБа¶Ща¶њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ඙аІБаІЬаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Њ ඙аІБаІЬаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ටගථග а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ аІ™а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගаІЯаІЗ а¶Ча¶Ња¶Ы඙ඌටඌ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පඌа¶∞аІНа¶Я ටඌа¶ХаІЗ а¶ХගථаІЗ බගа¶За•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ටගථග а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌаІЯ а¶ЂаІЗа¶∞ බаІЛа¶Хඌථ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЃаІБබග а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗථ ඲ඌථ, ඙ඌа¶Я, а¶Ъа¶Ња¶≤, а¶°а¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ а¶ХаІЯаІЗа¶Х බ඀ඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ, ‘а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≠а¶ња¶Яа¶ЊаІЯ а¶Ша¶∞ ටаІБа¶≤а¶ђа•§ а¶Єа¶Хගථඌа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶ња¶Яа¶ЊаІЯ ඕඌа¶Ха¶ђа•§’ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ටඌа¶∞ а¶ХඕඌаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶®а¶®а•§ ටඌа¶∞ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ЬаІАඐථ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З ඕඌа¶Ха¶ња•§ а¶Па¶Хබගථ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ බаІЛа¶ХඌථаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶≤аІЛа¶ХඪඌථаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ а¶Ъа¶Ња¶®а•§ а¶ПටаІЗ ටගථග а¶ХаІНа¶ЈаІБа¶ђаІНа¶І а¶єа¶®а•§ ටගථග а¶Жа¶∞ බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶ђа¶Єа¶ђаІЗථ ථඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ђ а¶ЬඌථගаІЯаІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶≠а¶ња¶Яа¶ЊаІЯ а¶ЦаІЬаІЗа¶∞ ‘а¶ђа¶Ња¶ЗපаІЛ’ (а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶Ша¶∞) а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶∞ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ПටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶ЦаІБа¶ђ а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶™а¶Ња¶®а•§ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ ඐථаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІО а¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶єаІБа¶БපගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗථ, ‘а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌаІЯ ඙ඌ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗ ඙ඌ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶ђаІЗ’а•§ а¶П а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶У а¶ЄаІО а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ђа¶ња¶ЪаІНа¶ЫගථаІНථ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§
а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථаІЗа¶®а•§ ටගථග а¶Єа¶ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶њ а¶ХගථаІЗ а¶ЖථаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶Ыа¶ња•§ ටගථග а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌаІЯ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ථ ඙ඌආගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ПටаІЗ а¶ђаІЗප а¶≤а¶Ња¶≠ а¶єаІЯа•§ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЧаІБа¶£ а¶ЧаІБа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Чඌථ а¶ЧаІЗаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶Жප඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶ЧඌථаІЗа¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞ а¶ђа¶Єа¶§а•§ ටගථග а¶∞ඌට а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Уа¶З а¶Єа¶ђ а¶Жа¶Єа¶∞аІЗа¶∞ а¶Чඌථ පаІБථаІЗ а¶≠аІЛа¶∞а¶∞ඌටаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Ђа¶ња¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶∞аІЗа¶ЧаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ха¶Ња¶Эа¶Ха¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶∞ඌට а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ а¶Чඌථ පаІЛථඌа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග ටගථග а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Йа¶Іа¶Ња¶У а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа¶®а•§
аІІаІѓаІЂаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ටඌа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ ‘а¶ђа¶ња¶ІаІБ’ а¶ђа¶њаІЬа¶ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶ђа¶ња¶ІаІБ а¶≠аІВа¶Ја¶£аІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНපаІЗ а¶ђа¶њаІЬа¶ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶њаІЬа¶ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ ටගථග ඃපаІЛа¶∞аІЗа¶∞ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Ша¶∞ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ ථаІЗа¶®а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ ‘а¶ђаІНа¶≤а¶Ња¶ХаІЗа¶∞ (а¶ЪаІЛа¶∞а¶Ња¶Ъа¶Ња¶≤ථ) ඙ඌටඌ а¶ХගථаІЗ ටගථග а¶ђа¶њаІЬа¶њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶П а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗ ඙аІБа¶≤ගප а¶Ха¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ѓа¶Є а¶Эа¶Ња¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞а¶§а•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶Эа¶ња¶Ха¶∞а¶Ча¶Ња¶Ыа¶Њ ඕඌථඌа¶∞ ඙аІБа¶≤ගප ටඌа¶ХаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗ ටගථග ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථаІЗථ а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶≤а¶Ња¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌටඌ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶њаІЬа¶њ ඐඌථඌඐаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටගථග ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯаІА а¶ЃаІЛа¶Ьа¶Ња¶єа¶Ња¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌаІЯ а¶ЪаІЛа¶∞а¶Ња¶З ඙ඕаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ ඙ඌටඌ ඐඌබ බගаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶њаІЬа¶њ ටаІИа¶∞а¶ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Яа¶ња¶З ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ђа¶њаІЬа¶њ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ ථඌඁаІЗ බаІЗපඐаІНඃඌ඙аІА а¶Па¶Цථ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ша¶∞аІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ьа¶ња¶Х а¶ЙබаІНබගථ а¶∞ඌට-බගථ аІ®аІ™ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬ а¶Ха¶∞а¶Ња¶®а•§ а¶Еа¶≤аІН඙ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ‘а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ђа¶њаІЬа¶њ’ а¶єа¶Ња¶Я а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶ђа¶њаІЬа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ ථаІЗපඌаІЯ ටගථග а¶ШаІЛа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ ඙а¶∞а¶ња¶ЄаІНඕගටග а¶Пඁථ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ, а¶ђа¶њаІЬа¶ња¶З ටඌа¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶њаІЬа¶ња¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶ЫаІБа¶ЯටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶Ь а¶Ца¶ђа¶∞ ථаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ථаІЗа¶За•§ аІІаІ¶/аІІаІЂ බගථ ඙а¶∞඙а¶∞ ටගථග ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ а¶ЖඪටаІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІЛаІЯඌටග а¶єа¶За•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЖථථаІНа¶¶а•§ а¶Па¶З а¶ЖථථаІНබ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඪථаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЖථථаІНа¶¶а•§ а¶ХගථаІНටаІБ පаІНඐපаІБа¶∞а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ХаІЗа¶Й ථඌ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЖථථаІНබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Вඐඌබ а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ а¶ЬඌථඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ ඙аІЛаІЯඌටග а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Па¶Х а¶ЧаІНа¶≤а¶Ња¶Є බаІБа¶І а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶°а¶ња¶Ѓ а¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓаІЗ а¶ЬаІЛа¶ЯаІЗа¶®а¶ња•§ а¶Ха¶ЪаІБа¶ШаІЗа¶ЪаІБ පඌа¶Ха¶Єа¶ђа¶Ьа¶њ а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Ѓа¶Ња¶Ы а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є а¶ЦаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටගථගа¶У ථගаІЯඁගට а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ца¶∞а¶ЪаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ аІІаІѓаІЂаІ™ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНටඌථ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Уа¶≤ඌථඌ ඙аІНа¶∞ඕඌ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА а¶Жа¶Ьඌථ බаІЗа¶®а•§ ටගථග ථඐа¶Ьඌටа¶ХаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗථ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНа¶¶а¶ња¶®а•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞а¶У а¶Х඙ඌа¶≤ ඙аІЛаІЬа¶Ња•§ ටඌа¶ХаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ ආගа¶Хඁට බаІБа¶І а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ බаІБа¶Іа¶З а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Е඙аІБа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶Ьථගට а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ බаІБа¶І а¶ЂаІБа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ටа¶Цථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ЈаІНа¶ЯаІЗ а¶Ча¶∞аІБа¶∞ බаІБа¶І а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З බаІБа¶І а¶Ъගථග а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Ча¶Ња¶Ѓа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ аІІаІ™ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞а¶У аІ™а¶Яа¶њ ඪථаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Њ а¶єа¶За•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЃаІЛඁගථа¶ЙබаІНබගථ, ඪඌ඀ගථඌ, а¶Жа¶Ђа¶ња¶≤ а¶У а¶ґа¶Ња¶єа¶ња¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІЛථ ඪථаІНටඌථа¶ХаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶Ы, а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶Є, а¶°а¶ња¶Ѓ, බаІБа¶І а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶ХගථаІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞ගථග а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІЗපග බаІБа¶ЯаІЛ а¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Ња•§
ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Њ ථඌඁа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЕථаІНа¶Іа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ටа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЬаІЛථඌа¶Ха¶њ ඙аІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІЛ, а¶Жа¶ХඌපаІЗа¶∞ ටඌа¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ පаІЛථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶єаІБටаІЛа¶Ѓ ඙аІЗа¶Ба¶Ъа¶Њ а¶Жа¶∞ පගаІЯа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха•§ а¶≠аІЯаІЗ а¶Ча¶Њ а¶Ыа¶Ѓа¶Ыа¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≠аІЯа¶ХаІЗ ටඌаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІЛаІЯа¶Њ බа¶∞аІБබ ඙аІЬаІЗ а¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶ЂаІБа¶Б බගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ња¶єа¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶З පගපаІБ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ ‘а¶ђа¶Ња¶ЗපаІЛ’ а¶Ша¶∞аІЗ а¶∞ඌට а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶∞ а¶Єа¶ња¶Бබ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ පаІЗа¶Ј а¶Єа¶ЃаІНа¶ђа¶≤ а¶ЪаІБа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ඪඌට බගථ, ඙ථаІЗа¶∞ බගථ ඙а¶∞඙а¶∞ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ а¶Жа¶ЄаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ца¶∞а¶ЪаІЗа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගаІЯаІЗ а¶Па¶Х а¶∞ඌට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ, ‘ටаІБа¶З а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ ඕඌа¶Ха•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ха¶∞а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶єа¶≤аІЗ а¶Ша¶∞ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛа¶ХаІЗ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа•§’ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ЖපаІНа¶ђа¶ЄаІНට а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶њ, ‘ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶ХаІЛථ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ша¶∞а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Ња¶ђа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗа¶У බаІЗа¶ЦаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ђа•§ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯ ඁථ බඌа¶Уа•§ а¶ЙථаІНථටග а¶Ха¶∞а•§ а¶ЖаІЯ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а•§’ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ аІ© а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶Є ටа¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНටඌථ а¶ЃаІЛඁගථ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Ха¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බаІБа¶І, а¶ЂаІЗථ, а¶Жа¶Яа¶Њ а¶ЧаІЛа¶≤а¶Њ а¶Ца¶Ња¶ЗаІЯаІЗ බаІБа¶З а¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ බаІБа¶З а¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ බаІБа¶З ඙ඌපаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗ පаІБаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶≠аІЯ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඃබග පගаІЯа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ, а¶ЃаІЛඁගථа¶ХаІЗ а¶ЯаІЗථаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ යඌටථаІЗаІЯ (а¶ђа¶Ња¶∞ඌථаІНබඌ) а¶ЃаІЛඁගථа¶ХаІЗ а¶ђаІЗබаІЗ ඙ඌа¶ЯගටаІЗ පаІБа¶ЗаІЯаІЗ ඙ඌපаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ђа¶Єа¶њаІЯаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЦаІЬа¶њ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞аІЗටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶°а¶Ња¶≤, ඙ඌටඌ а¶ХаІБаІЬа¶њаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶З බගаІЯаІЗ а¶≠ඌට ටа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶∞ඌථаІНථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ ඪඌට а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶ЯаІБ ඪඁඌථ а¶єа¶Ња¶ђаІЬаІЗ (а¶ХඌබඌаІЯ) а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ХаІЛа¶≤аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ ඙аІЗаІЧа¶Ба¶ЫаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞බаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња•§ ටඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЕථаІБа¶∞аІЛа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, ‘а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶Ь а¶Ца¶ђа¶∞ ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ЦаІЗа¶Ња¶Ба¶Ь а¶Ца¶ђа¶∞ а¶®а¶ња¶ђа¶Ња•§ ටඌа¶ХаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІЬа¶Ња¶ђа¶Њ’а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠аІЗа¶Я ඙аІЬඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶ХаІЗපඐа¶≤а¶Ња¶≤а¶ХаІЗ ආගа¶Х а¶Ха¶∞а¶ња•§ ටගථග а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ඙аІЬඌටаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗපඐа¶≤а¶Ња¶≤ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ЃаІЛඁගථа¶ХаІЗа¶У ඙аІЬа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪථаІНටඌථබаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞а¶ђа¶њ ඙аІЬа¶Њ පගа¶Ца¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථග පа¶∞аІАа¶Ђ ඙ඌආ а¶Ха¶∞ටаІЗ පගа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ ථඁаІНа¶∞, а¶≠බаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ පаІБа¶®а¶§а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ බаІЛа¶Хඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІЗа¶≤, ථаІБථ а¶ХගථаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටඌඁ, ‘බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Єа¶ђа¶Ња•§ බаІЛа¶ХඌථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Њ බගඐඌ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶ђа¶Њ а¶®а¶Ња•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁගපඐඌ а¶®а¶Ња•§’ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЯ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶ЂаІБа¶≤ටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶ЯаІЗ а¶ѓаІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶®а¶§а•§
а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ аІ≠ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶Є ටа¶Цථ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ђа¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶Ша¶ЯථඌаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඁථаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІНඃඕඌ ඙ඌа¶За•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ, а¶ЃаІЛඁගථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІЛа¶Ъа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІЗа¶БබаІЗ а¶ХаІЗа¶БබаІЗ а¶ђаІБа¶Х а¶≠а¶Ња¶Єа¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶њаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Эа¶ЧаІЬа¶Ња¶Эа¶Ња¶Яа¶њ а¶Ха¶∞а¶ња¶®а¶ња•§
а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Цථ аІЃ/аІѓ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶Є ටа¶Цථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛа¶≤ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ ටඌа¶ХаІЗ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ, ‘а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§ а¶Уа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ а¶Уа¶∞ ථටаІБථ а¶Ѓа¶Њ а¶Уа¶ХаІЗ а¶Жබඌа¶∞ ඃටœ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ පගа¶Ца¶Ња¶ђаІЗа•§’ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ ඁඌථаІБа¶Ј а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ පගа¶Ца¶ђаІЗа•§ а¶П а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ බаІЗа¶За¶®а¶ња•§ ටඐаІЗ а¶єа¶Ња¶Йа¶Ѓа¶Ња¶Й а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶БබаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Уа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶Уа¶ХаІЗ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є а¶ЯаІБටаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ ඙а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶°а¶Ња¶Ща¶ЊаІЯ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ බаІЗа¶Ца¶њ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ШаІНඃඌථඌ (а¶∞аІЛа¶Ча¶Њ) а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЦаІБපගටаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Іа¶∞а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶Ха¶њ! ඁපඌ а¶Ха¶Ња¶ЃаІЬ බගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ЂаІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶∞ පа¶∞аІАа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЗа¶∞ ඁට а¶Ха¶Ња¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЬඌථටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶њ, ඁපඌа¶∞а¶њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ පаІЛаІЯඌථаІЛ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌට а¶ХаІБаІЯа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌථග ටаІЛа¶≤ඌථаІЛ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶ђа¶Яа¶њ බගаІЯаІЗ ටа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶У а¶ХаІЛа¶ЯඌථаІЛ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Єа¶ђ а¶ЬаІЗථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, ‘а¶ђа¶Ња¶За¶ЪаІЗ ඕඌа¶Хටග ටаІЛа¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ ඃඌටග බаІЗа¶ђ а¶®а¶Ња•§’ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Эа¶ЧаІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, ‘ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඲ඌථ а¶≠а¶Ња¶®а¶ђа•§ ඲ඌථ ඪගබаІНа¶Іа¶Њ පаІБа¶ХථаІЛ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶ђа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶≠ඌට а¶Хඌ඙аІЬ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶ђа•§ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Ца¶∞а¶Ъа¶У බаІЗа¶ђа•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶П ථගаІЯаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථ බගථ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ ථඌа¶≠а¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§’ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Жа¶∞ а¶ЃаІЛඁගථа¶ХаІЗ බаІБа¶З а¶ХаІЛа¶≤аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЪаІБа¶ЃаІБаІЯ а¶ЪаІБа¶ЃаІЯ а¶Ча¶Ња¶≤ а¶≠а¶∞а¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц බගаІЯаІЗ බа¶∞බа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ඙ඌථග ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ බаІБа¶З а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ХаІЗ ටඌ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ බගа¶За¶®а¶ња•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЂаІЗа¶Ња¶БаІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶З а¶ЂаІЗа¶Ња¶БаІЬа¶Ња¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶∞ඌටаІЗ а¶ШаІБඁඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХඌථаІНථඌа¶Ха¶Ња¶Яа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ පගපаІБ а¶ЃаІЛඁගථ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІА а¶Еථගа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞ඌටаІЗ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ѓаІЗаІЯаІЗ а¶Ѓа¶Ва¶≤а¶Њ ආඌа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Уа¶ЈаІБа¶І а¶ПථаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Х බඌа¶Ч а¶Па¶Х බඌа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Уа¶ЈаІБа¶І а¶ЦаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІНඃඕඌ а¶Ха¶Ѓа¶≤аІЗа¶У а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶Ња¶БаІЬа¶Ња¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Еа¶ЄаІБа¶ЄаІНඕ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛа¶Ха¶Ѓа¶Њ а¶≠а¶ња¶Ьа¶њаІЯаІЗ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶єаІЯ, а¶ЂаІЗа¶Ња¶БаІЬа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЈаІНа¶Я බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ, а¶ЃаІЛඁගථа¶У а¶ХаІЗа¶БබаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЂаІБа¶≤ටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Уа¶ЈаІБа¶І ථඌ බගаІЯаІЗ а¶ЦаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ЈаІНа¶ЯаІЗ аІІаІ¶аІ¶ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ЬаІЛа¶Ча¶ЊаІЬ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІА а¶Жа¶≤аІА а¶єаІЛа¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЦаІБа¶≤ථඌа¶∞ а¶ђаІЬ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ ඙ඌපග а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ ටගථග а¶ЂаІЗа¶Ња¶БаІЬа¶Њ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ ඙аІБа¶Ба¶Ь а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶П а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ђа¶њ බඌඐග а¶Ха¶∞аІЗථ аІІаІЂаІ¶ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ටаІЛ а¶Па¶З а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථаІЗа¶За•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ аІІаІ¶аІ¶ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ බගа¶За•§ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ аІЂаІ¶ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථඌ බගаІЯаІЗ ඙ඌපග а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶∞‘ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§ а¶ЦаІБа¶≤ථඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Йа¶†а¶ња•§ а¶ХථаІНа¶°а¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶≠а¶ЊаІЬа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ХаІЛඕඌаІЯ ඙ඌඐ ? බаІЗа¶ђ බаІЗа¶ђ а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶ђа¶Ња¶Є а¶ЂаІБа¶≤ටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЗඁඌථаІА а¶Єа¶∞බඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶УආаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶≠а¶ЊаІЬа¶Њ බගа¶За•§ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђаІЬ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶П а¶Хඕඌа¶У а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, ‘а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЦаІБа¶ђ а¶¶а¶Ња¶Ѓа•§ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а•§ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ යටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§’ а¶ЂаІЗа¶Ња¶Ња¶Б а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶Ха¶ња¶Ь а¶ЙබаІНබගථ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Па¶≤аІЗ ටඌа¶ХаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ша¶Яථඌ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ђа¶≤а¶ња•§ ටගථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ පаІБථаІЗ а¶Жථඁථඌ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶ЪаІБ඙ а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ ටගථග а¶ђа¶≤аІЗථ, ‘а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ-а¶Ѓа¶Њ ඐගථඌ а¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶ЊаІЯ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටаІБа¶За¶У а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶њ බගටаІЗ ථඌ ඙аІЗа¶∞аІЗ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶≤а¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З а¶єаІЛа¶Х а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ ඐඌථඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ඙аІЯа¶Єа¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ча¶∞а¶ња¶ђ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ යඌඪ඙ඌටඌа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ђа•§’
а¶Па¶Хබගථ බаІЗа¶Ца¶њ, а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ ? а¶ХаІЗ ටаІЛа¶ХаІЗ а¶ЃаІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗ ? ඙аІЬа¶Њ ඙ඌа¶∞ගඪථග ? а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІЗට බගаІЯаІЗ ඙ගа¶Яа¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ? а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Ха¶Ња¶БබටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЗ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ බаІЗаІЯ а¶®а¶Ња•§ පаІБа¶ІаІБ а¶Ха¶Ња¶БබаІЗ ඥаІЛа¶Х а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞ටග ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ ‘а¶Ха¶≤а¶Ѓ, а¶Ха¶≤а¶Ѓ’а•§ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ, ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІА ටඌයаІЗа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථටаІБථ а¶Ха¶≤а¶Ѓ ථගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶Эа¶ЧаІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗ ඙аІЬаІЗ ටඌයаІЗа¶∞а•§ ටඌයаІЗа¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶≤а¶Ѓ ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶≤а¶Ѓ බගаІЯаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ ටඌයаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ѓ а¶ХаІЗаІЬаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ, ‘ටаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටථ а¶Ха¶≤а¶Ѓ а¶ХගථаІЗ බගටаІЗа•§’ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶З а¶Хඕඌ පаІБථаІЗ а¶Па¶Х යඌටаІЗ බඌ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х යඌටаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ යඌට а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЫаІБа¶ЯටаІЗ ඕඌа¶Ха¶ња•§ а¶ђа¶Ња¶Бප а¶ђа¶Ња¶ЧඌථаІЗ а¶ѓаІЗаІЯаІЗ а¶ХаІБа¶ЮаІНа¶Ъа¶њ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ ටගථ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶Ха¶≤а¶Ѓ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶њ, ‘а¶Па¶З ථаІЗ ඐඌ඙ а¶Ха¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ ටаІЛа¶∞ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗ а¶Ха¶Ња¶≤а¶њ а¶ЂаІБа¶∞а¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§’ а¶ХаІБа¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ѓ යඌටаІЗ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶ЦаІБපගටаІЗ ථаІЗа¶ЪаІЗ а¶УආаІЗа•§ ටඌа¶∞ а¶ХඌථаІНථඌ ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶≤а¶Ѓ යඌටаІЗ а¶ЫаІБа¶Я බගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ, ‘ටඌයаІЗа¶∞ ටаІЛа¶∞ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≠аІБа¶Ха¶њ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Њ а¶ХаІБа¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ѓ ඐඌථඌа¶З බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІБа¶ЮаІНа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶ђа•§ ටаІЛа¶∞ а¶Ха¶≤а¶Ѓ а¶ЫаІЛа¶ђ а¶®а¶Ња•§
а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ ඙ඌථගа¶∞ а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІА а¶єа¶Ња¶ЄаІЗа¶Ѓ а¶Жа¶≤аІА පаІЗа¶ЦаІЗа¶∞ ඙аІБа¶ХаІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶≤а¶ЄаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ ඙ඌථග а¶ПථаІЗ а¶∞ඌථаІНථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶§а¶Ња¶Ѓа•§ ටඐаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶Х а¶Ха¶ња¶≤аІЛа¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ බаІВа¶∞ а¶ЬаІБаІЬаІЛа¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Я а¶Иබа¶Ча¶Ња¶єаІН а¶ЃаІЯබඌථаІЗа¶∞ а¶Яа¶ња¶Йа¶ђа¶УаІЯаІЗа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඌථග ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶ЯаІБ ඪඁඌථ а¶Хඌබඌ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඌථග а¶ЖථටаІЗ а¶ѓаІЗаІЯаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶≤а¶Є ථගаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ЊаІЯ а¶ђаІНඃඕඌ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶∞඙а¶∞а¶У ඙аІНа¶∞ටගබගථа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ЪඌබаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Р а¶Ха¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඌථග ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња•§ ඙ඌථග а¶Жථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Хබගථ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶≤а¶Є а¶ХаІЗаІЬаІЗ ථගаІЯаІЗ ඁඌඕඌаІЯ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶≤а¶Є а¶≠а¶∞аІНටග ඙ඌථග а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ථගаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ, ‘а¶Ѓа¶Њ а¶Ха¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶З ඙ඌථග ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђа•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ ඙ඌථග а¶ЖථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§’ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌටаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶њ а¶єа¶За¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, ‘а¶ЄаІЛථඌ ටаІБа¶Ѓа¶њ ඁථ බගаІЯаІЗ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඙ඌථග а¶ЖථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ЭаІЬ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х ඙ඌථග а¶Жа¶Ѓа¶ња¶З ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђа•§’ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶∞аІНа¶Ја¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ аІЃ/аІІаІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤а¶Х а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЙබаІНබගථ а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶Ха¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌථග а¶ПථаІЗ බගаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЈаІНа¶Я බаІВа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗ-
( ඙аІНа¶∞аІЯඌට а¶Ђа¶Ца¶∞аІЗ а¶Жа¶≤а¶ЃаІЗа¶∞ ‘а¶Ѓа¶Њ а¶Єа¶Хගථඌ’ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗаІЯа¶Њ)